এখনও অনেকের পাতে নিয়মিত আমিষ জুটে না, তবে ক্ষুধায় মারা যাওয়ার খবর শোনা যায় না।
রাজু আহমেদ, প্রাবন্ধিক।
যিনি মাসের শেষে নিয়ম করে মজুরি পান, তার কাছে জীবিকা অর্জন মামুলি ব্যাপার। খদ্দের বা মক্কেল পেলেই যাদের পকেট ফুলে ওঠে, তাদের কাছে জীবিকা নির্বাহের এমন প্রশ্ন করলে তারা হেসে উড়িয়ে দেবে। সরকারি কর্মীর কাছে—কাজ থাকুক বা না থাকুক—বেতন যার খাড়া, তার কাছে এসব কিছুই চিন্তার বিষয় নয়। যার কাছে দক্ষতা আছে, সে সেটা বিক্রি করে চলে যেতে পারে। কিন্তু যে মজদুর দিনের শ্রমে দিন গুজরান করে, তার একদিনের অসুস্থতা বা শরীর দুর্বল হয়ে আসা মানেই জীবিকা কঠিন হয়ে ওঠা। শহরে গোলাপ বা বাদাম বিক্রেতার রিজিকও অন্যের পকেটে বাঁধা—শহরবাসীর মন খারাপ হলে বা প্রেম ভোলার দিনে ফুল বিক্রেতাকে পেটে পাথর বেঁধে থাকতে হয়।
আশি বছরের ভিক্ষুক দম্পতি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অন্যের পানে হাত বাড়িয়ে রাখে। করুণা হলে কেউ পকেটের সবচেয়ে ছোট নোটটি ফেলে দেয়, তাও সবাই না। মানুষের মায়া কমছে, মানবিকতা হারিয়ে যাচ্ছে, আর ভিক্ষাবৃত্তি অনেকের পেশা হয়ে উঠছে—এ অবস্থায় পরকালের সওদা কেনাও থেমে যেতে পারে। বরফ বিক্রেতার মূলধন বাতাসেই গলে যায়, ক্ষতিও তাই নিশ্চিত। কার রিজিক মওলা কোন পকেট থেকে বের করেন, তা বড় রহস্য। কান-পরিষ্কারক অপেক্ষা করে বাস বা রেলস্টেশনে—বাস দেরি করে, রেল লেইট করে বলেই কোনো যাত্রীর পকেট থেকে দশ টাকার নোট বের হয়ে তার সংসারের চাল-ডালের জোগান হয়।
এখনও অনেকের পাতে নিয়মিত আমিষ জুটে না, তবে ক্ষুধায় মারা যাওয়ার খবর শোনা যায় না। সময় বদলেছে। নব্বই দশকের গোড়ায় গাঁও-গেরামে পেটে ভাতের চুক্তিতে কামলা পাওয়া যেত। তারও আগে ভাতের মারের জন্য বড় ঘরে মালশা জমতো—গিন্নী দয়ালু হলে সঙ্গে কয়েকটি ভাতও দিতেন। সেই ভাতেই বেঁচে থাকতো পরিবারের ছোটরা। অথচ এখন উচ্চ পারিশ্রমিক দিয়েও শ্রমিক পাওয়া যায় না। ছোট শহরে লাখ লাখ মানুষ, কিন্তু দৃশ্যত কেউ বেকার নয়। রিকশার দশ-বিশ টাকার ভাড়া জমে চালকের দৈনিক আয় হাজার ছাড়িয়ে যায়। গ্রামে কৃষি শ্রমিকের অভাবে সবজির দামও শত ছুঁইছুঁই।
জ্যান্ত কাঠের কত গভীরে পোকা আছে তা কাঠঠোকরা ঠিকই জানে, কিন্তু মানুষ দুই ইঞ্চি সামনের ভবিষ্যতও দেখতে পায় না—তবু পরিশ্রম করে যায়। যে জুতা সেলাই করে, সে আসলে নিজের কপালই সেলাই করে! অন্যের পায়ের দিকে তাকিয়ে থেকেও যার দৈনিক আয় হাজার টাকা, তাকে শুধু অপেক্ষা করতে হয়। নরসুন্দর, ধোপা, ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারক—কোনো পেশাকেই তুচ্ছ বলার সুযোগ নেই। প্রত্যেকের পেশার আড়ালে রিজিক লুকিয়ে থাকে—শুধু তার নয়, তার ওপর নির্ভরশীল সবার জন্যও। পার্থক্য শুধু এই—কেউ দুশ্চিন্তায় দিন শেষ করে, কেউ থাকে নিশ্চিন্তে।
কারো কারো রিজিকে রহস্য, আবার সে রহস্যও রহস্যে ঘেরা। রাখালের কথাই ধরুন—পশুর রিজিক নিশ্চিত করে সে নিজের রিজিকেরও নিশ্চয়তা পায়। যে হোটেলে অন্যকে খাইয়ে উপার্জন করে, তারপর নিজে খায়—তার বাস্তবতাই বা কেমন? মানুষের খাবারের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর, অথচ সিংহভাগ পূরণও হচ্ছে নিয়মিত। একদিনের খাবারের তালিকা নিয়ে গবেষণা করলেই চমকে উঠতে হবে। সারা পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে একেকটি উপকরণ এসে মিলিত হয়ে তৈরি হয় একটি ডিশ।
যে চালের ভাত, যে পানির মাছ, যে মাটির সবজি আর যে গাছের তেল—সবই দেশব্যাপী বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন উৎস থেকে আসে। গরুর দুধ আর আখের গুড়—কত দূর পেরিয়ে এসে একত্র হয়! যে কেবল আলুভর্তা পেয়েছে, তার আলু কোথা থেকে এসেছে, মরিচ কোথা থেকে, আর পিঁয়াজই বা কোথা থেকে? লবণের উৎস হয়তো কোনো সমুদ্রের তীর। কী আশ্চর্যজনকভাবে মানুষ বেঁচে আছে! বাঁচার জন্য যে অক্সিজেন লাগে, তা কীভাবে উৎপন্ন হয়, কোন পথে আসে, আর কার্বন-ডাই-অক্সাইডই বা কীভাবে চলে যায়—তা নিয়ে ভাবলেই বিস্ময় জাগে। বিচিত্রতর চিন্তার সব উৎস ও উপকরণ প্রকৃতিতেই আছে। এগুলো অস্বীকার করা মানে নিজের অস্তিত্বকেই উপহাস করা।
যে-জন বৃদ্ধ বয়সে এখনো জীবনের ঘানি টানে এবং যে তরুণ এখনো অন্যের ওপর নির্ভরশীল—কার অবস্থান ভালো, বলা কঠিন। বাস্তবতা এমন যে ছয় বছরের শিশুকেও সংসারের দায়িত্ব নিতে হয়, আবার কেউ ষাট বছরেও বাবার সম্পদ বিক্রি বা ভাড়া দিয়ে খায়। দরিদ্রের হতাশা এবং ধনীর প্রত্যাশা দুটোই অস্থিতিশীল। সম্পদ চক্রাকারে ঘোরে—আজকের ফকির পরিশ্রমে ধনী হতে পারে, আর সকালের ধনী সন্ধ্যায় ফকির হয়ে যেতে পারে। জীবন ও জীবিকা একপ্রকার জুয়া। তাই সামর্থ্যের মধ্যে সন্তুষ্টি, অবস্থানে প্রশান্তি এবং ভাগ্যে যা আছে তাতে কৃতজ্ঞ থাকাই শ্রেয়। ভাগ্যে না থাকলে জোর করেও নাগালের মধ্যেরও অনেক কিছু পাওয়া যায় না।

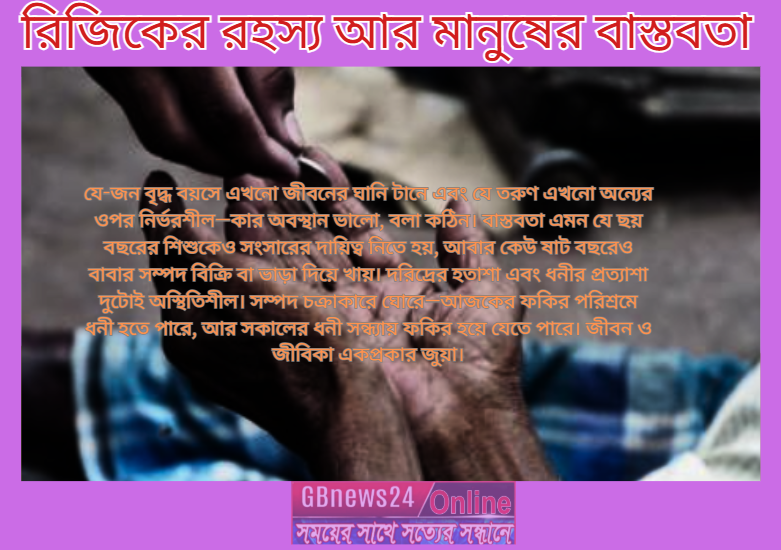





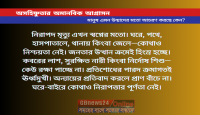
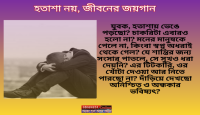


মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন