রাজু আহমেদ, কলাম লেখক।
ধারণা করা যাচ্ছে, ছাব্বিশের ফেব্রুয়ারির পরে ড. মুহাম্মদ ইউনূস অধ্যায় বাংলাদেশের অতীত। যে স্বপ্ন নিয়ে তিনি এসেছিলেন কিংবা আহ্বান করে আনা হয়েছিল মোটাদাগে, সেসবের অনেক কিছুই পূরণ হয়নি—আর আলামত বলছে, হবেও না অনেকখানি। এজন্য দায়ী কারা? এককভাবে কেউ নয়; বরং অল্পবিস্তর সবাই দায়ী। যাদের হাত ধরে জুলাই অভ্যুত্থান ঘটেছে, তারাও দায়ী। রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার লাভের সম্ভাবনা অনুযায়ী দায়ী। মোটকথা, বাংলাদেশের ভাগ্য সেই পুরোনো অবস্থানেই আটকে আছে।
আপনার দৃষ্টিতে সবচেয়ে ভালো মানুষ, দেশপ্রেমিক মনোভাবসম্পন্ন রাজনৈতিক দলটিও যদি ক্ষমতায় আসে, তবুও সেটি পুরোনো মডেলই অনুসরণ করতে পারে। হয়ত করবেও। ভিন্নতর নতুন কিছুর আশা নেই। মানুষগুলোর শুধু চেহারা বদলাবে, কিন্তু চরিত্র বা নীতি তথা দুর্নীতি, কুনীতি সেই আগেরটাই বহাল থাকতে পারে বা থাকবে। যে দলই ক্ষমতায় আসুক, পরাজিত প্রত্যেকটি দল ক্ষমতাসীন দলের নগ্ন বিরোধিতা করবে। প্রত্যেকটি কাজের সমালোচনা এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার প্রবণতা থাকবে। ফলে শাসকদলকে আবার দমননীতি গ্রহণ করতে হবে। ক্ষমতাসীনরা বিরোধীপক্ষের পরামর্শের সবকিছু অবজ্ঞা করেন। তখন ট্যাগিং ও চেতনার ব্যবসা চালু রাখার প্রয়োজন হবে। ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতার বাইরে থাকা কেউ-ই প্রকৃতপক্ষে একে অপরের বন্ধু হবে না।
ড. ইউনূসের সামনে সুযোগ ছিল—সব রাজনৈতিক দলের হাত একত্র করে শহিদ ও আহতদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার। ঘুষ-দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং স্বৈরতান্ত্রিক বাংলাদেশ আমরা চাই না। জুলাই যোদ্ধারা যে বিরল সুযোগ এনে দিয়েছিল, জাতি তা শেষ পর্যন্ত ইয়ার্কিতে উড়িয়ে দিয়েছে। কারো বেতন বাড়াতে হবে, কারো সুযোগ-সুবিধা লাগবে, কারো জাতীয়করণ প্রয়োজন, কাউকে জুলাইয়ের একক মালিকানা দিতে হবে— শত সহস্র আন্দোলনের ভিড়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ মাসের মধ্যে পাঁচটি সিঙ্গেল দিনও নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারেনি। দুনিয়ার যত দাবিদাওয়া—কাজর বেটি থেকে রাষ্ট্রপতি বদলানো পর্যন্ত—সবই এই সময়টাতে উঠে এসেছিল এবং তা রাজপথে। রাস্তা আটকে, সচিবালয়ে হামলে পড়ে কত রকমের বাহানা! গুজবের ডালপালা কতভাবে যে কতদিকে ছড়িয়েছিল। দেশবিদেশের বহু মাথার ষড়যন্ত্র সামলে ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকার যতটুকু আসতে পেরেছে, এখনো অন্তত বিষাদ মুখে হাসতে পারছে—সেই তো অনেক! জাতির উদ্দেশ্যে গতকালের ভাষণে অনেক হতাশার ইঙ্গিত পেলাম।
এই বাংলাদেশ ড. ইউনূসকে আর দ্বিতীয়বার নাও পেতে পারে। যারাই নির্বাচিত হোক, তাদের জন্য আগামীর বাংলাদেশ পরিচালনা মোটেই সহজ হবে না। ক্ষতগুলো শুকায়নি; কিন্তু ক্লাসরুমে শিক্ষকের লেকচার শোনা এবং পরীক্ষার টেবিলে বসা চোখগুলো এখনও ভীষণ সচেতন। কানগুলো আহ্বান শোনার অপেক্ষায়। যারা একবার পথে বের হয়েছে তারা ঘরের চেয়ে পথের বেশি আপন হন। কারো জান জীবন নিয়ে, জেলে দিয়ে, সত্য বচন ও ভাষণ থেকে সরানো সম্ভব নাও হতে পারে। যারা সরকার গঠন করবে, তাদেরকে বহুমুখী শত্রু ও প্রতিপক্ষ মোকাবিলা করতে হবে। সামলাতে হবে পারে আন্তর্জাতিক চাপও। একগাদা ঋণের বোঝা রোজ চোখ রাঙাবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যদি শুধু ড. ইউনূস না থাকতেন, তবে গত এক বছরে কতবার পাল্টা অভ্যুত্থান হয়ে যেত, তা অনুমান করেও সংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের চক্রান্ত থেমে নেই। উগ্রপন্থিদের বিচরণেও কোনো বিশ্রাম নেই। মোটকথা, ধোঁয়াশা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে জাতি ও রাষ্ট্র। আমাদের অনাগত দিনগুলো কেমন হবে?
ড. ইউনূস ছাড়া অন্য কেউ ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের কথা বললে তা হয়ত বিশ্বাসযোগ্য হতো না। এখন নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চিতের কাছাকাছি। কোনো দৈব দুর্ঘটনা না ঘটলে ঈদের আগেই হবে ভোট। ক্ষমতায় একদল যাবে। পতিতরা রূপ পাল্টে সরাসরি ফিরে আসতে চেষ্টা করবে কিংবা কাউকে আশ্রয় করে দাঁড়ানোর কৌশল নেবে— কোন পথ নেবে সেটা ভবিষ্যৎই দেখাবে। তবে রাষ্ট্রের এই পরিস্থিতি—সংস্কার ও বিচারকে গন্তব্যে পৌঁছে না রেখে—নির্বাচনের আয়োজন, দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকা দলগুলো কতটা সামলাতে পারবে, তা নিয়েই রচিত হতে পারে নতুন ইতিহাস। অসম্পূর্ণ অভ্যুত্থান হাঁটতে পারে সম্পূর্ণতার দিকে। টালমাটাল বিশ্বপরিক্রমা তাই বলছে।
নির্বাচিত সরকারের অংশ হয়েও যদি ড. ইউনূসের সেবা গ্রহণ করা যেত, তবে বাংলাদেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে যেতে পারত। কিন্তু নির্বাচন দিয়ে ড. ইউনূস হয়ত একেবারেই এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারেন—তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং বক্তব্য সেই সম্ভাবনার দিকেই ইঙ্গিত দেয়। উন্নত চরিত্রের অধিকারীগণ প্রচণ্ড আত্মসম্মানের অধিকারী হন। দেশ গড়ার আশা ভঙ্গের পরে ইউনূস আর ফিরবেন? যারা স্বপ্নে বুক বেঁধেছিল, আশা ও আস্থা রেখেছিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ওপর—শেষমেশ নৈরাশ্যই তাদের ভরসা হয়ে উঠতে পারে। বিশ্লেষকরা শুরু থেকেই বলে আসছিলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তথা ড. ইউনূসের টিমে কয়েকজনকে বদলানো প্রয়োজন ছিল। তবে অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষা ও প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং অর্থসম্পদ পাচার প্রতিরোধে অল্প সময়েই আশানুরূপ কিছু অর্জিত হয়েছে। কমেছে বৈদেশিক ঋণ, বেড়েছে রাষ্ট্রীয় রিজার্ভ। দ্রব্যমূল্য হয়েছে সহনীয়। রাজনৈতিক দলগুলো এবং হয়ত অসহযোগিতায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সময়ের আগা-গোড়াই দুর্বল ছিল। অবশ্য স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মহোদয়কে এককভাবে দোষ দেওয়া যায় না—তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। তার মুভমেন্ট বলছে, তিনি সততার সাথেই লড়ে গেছেন।
সংস্কারের নামে ভাসা ভাসা কয়েকটি নীতিমালা নির্ধারণ করে গেলেই কাজ হবে না। বরং তাতে যে-ই সে-ই! ’৭২-এর সংবিধান দলীয় সংবিধানের ভূমিকাই পালন করেছে।অবশ্য এটা তখন একটি নির্দিষ্ট দলেরই স্বার্থ রক্ষায় রচনা। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সে-সকল অনুচ্ছেদে আপত্তি করেছিল তা মানা হয়নি, গুপ্তও স্বাক্ষর করেনি। ৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রতিটি শাসকগোষ্ঠীকেই স্বৈরাচার হওয়ার প্রলোভনে ফেলেছে। ন্যায়পাল এখনও কাল্পনিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। আরও বড় কিছু পরিবর্তনের সুযোগ ছিল, কিন্তু নানা শ্রেণির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অসহযোগিতায় তা সম্ভব হয়নি।
যারা সবকিছুর বাস্তবায়নের সক্ষমতায় ছিলেন, তারা হঠাৎ রাজনৈতিক দল গঠন করে নির্দিষ্ট একটি পক্ষে পরিণত হয়ে গেছেন। পরবর্তীতে নির্বাচিত দলটি “পতিত সরকারের” চেয়ে কতটা উত্তম হতে পারবে—তা বিদ্যমান ব্যবস্থা ও পরিস্থিতিতে অনুমান করা কঠিন, আশা করাও অশোভন হবে। এবারও জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ না-ও হতে পারে। অভ্যুত্থান পূর্ণাঙ্গ করতে না পারার খেসারত বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং জুলাই আন্দোলনের অংশীদারদের মেটাতে হবে। একটি রাজনৈতিক দলও এই মুহূর্তে তাদের কর্মী-সমর্থকদের কেন্দ্রীয় নির্দেশনা মানাতে পারছে না। নির্বাচনের পরে এই বিশৃঙ্খলা আরও বেগবান হয়ে উঠতে পারে। এমনকি নির্বাচনও হয়ে উঠতে পারে সহিংস! আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না করে নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট করা কতটুকু যৌক্তিক হচ্ছে তা বিবেচনা দরকার।


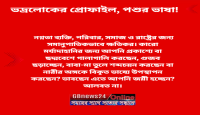
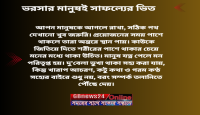

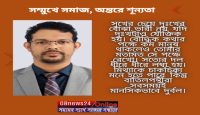
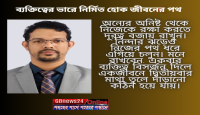


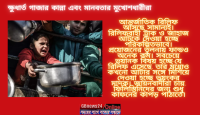
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন